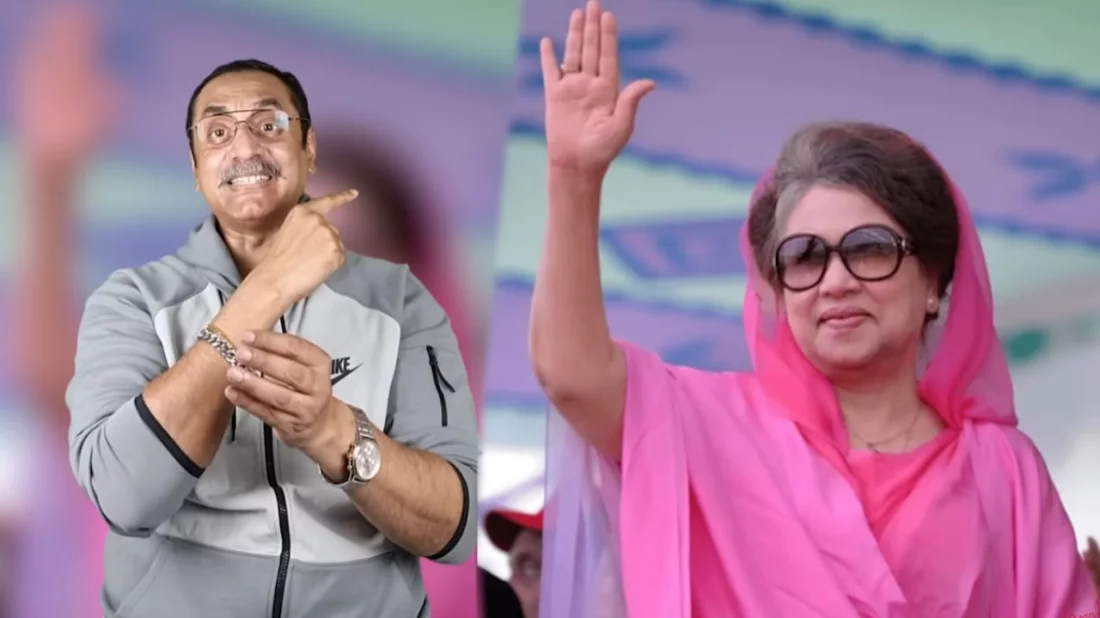কালাকানুন’ নাকি সংস্কার? সরকারি চাকরি সংশোধনী আইন ঘিরে বিতর্ক
- Update Time : ০২:১৪:৫৯ অপরাহ্ন, রবিবার, ২৫ মে ২০২৫
- / ১০৬ Time View

নির্বাচনকালীন সরকার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সম্প্রতি অনুমোদিত ‘সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ নিয়ে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তা শুধু একটি আইন বা বিধির বিরুদ্ধে ক্ষোভ নয়—এটি বাংলাদেশের কর্মপরিবেশ ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের অসামঞ্জস্যতার প্রতিচ্ছবি।
বাংলাদেশে প্রতিটি চাকরির—হোক তা সরকারি, বেসরকারি কিংবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে—অধিকার যেমন আছে, তেমনি রয়েছে কর্তব্য এবং জবাবদিহিতা। তবে বাস্তবতা হলো, কর্মক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ, জবাবদিহিতা এবং দায়িত্বশীলতা এখনও অনেকাংশে কাগুজে রয়ে গেছে। বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে কর্মরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হলেও বাস্তব প্রয়োগে দেখা যায় পক্ষপাতদুষ্টতা, দীর্ঘসূত্রিতা এবং অনিয়ম।
সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত ‘সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর খসড়াকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্নগুলো আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। আইনটির বিরুদ্ধে গত কয়েক দিন ধরে সচিবালয়ে হাজার হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী দপ্তর ছেড়ে বিক্ষোভ করেছেন। তারা এই অধ্যাদেশকে ‘কালাকানুন’ আখ্যা দিয়ে প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন। এই আন্দোলন কোনো সাধারণ বেতনবৃদ্ধি বা সুযোগ-সুবিধার দাবিনির্ভর নয়, বরং এটি একটি মৌলিক ও গভীর শঙ্কার বহিঃপ্রকাশ—চাকরিজীবীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন।
অধ্যাদেশটি কী বলছে?
সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর কিছু বিধান সংশোধন করে তৈরি এই খসড়া অধ্যাদেশে কিছু ‘নিবর্তনমূলক’ ধারা যুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে—
- কর্মচারী কর্তব্যে অবহেলা বা অসদাচরণ করলে তাদের বিরুদ্ধে সহজে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
- কোনো ধরনের শুনানি ছাড়াই সাময়িক বরখাস্ত বা চাকরিচ্যুতির ক্ষমতা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।
- প্রক্রিয়াগত জটিলতা এড়াতে ‘ত্বরিত বিচার’ ব্যবস্থার মতো নিয়ম যোগ করা হয়েছে যা অসদ্ব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি বহন করে।
বর্তমান কর্মচারীদের অভিযোগ, আধুনিক সময়ের জন্য এই ধারা অত্যন্ত অমানবিক এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী। তারা বলছেন, এই অধ্যাদেশ সংবিধানের ২৬, ২৭ ও ৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী, যেখানে সমতা, ন্যায্যতা ও আইনগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
বাস্তবতা: জবাবদিহিতার অভাব নাকি বৈষম্য?
বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি চাকরিতে কিছু অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। নিম্নস্তরের কর্মচারীরা নানা কারণে শাস্তি পেয়ে থাকেন, কিন্তু উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রায়শই দায় এড়াতে সক্ষম হন। উদাহরণ হিসেবে, ফাইল আটকে রাখা, ঘুষ নেওয়া, দাপ্তরিক বিলম্ব—এসব বিষয়ে শত শত অভিযোগ জমা থাকলেও, প্রকৃত শাস্তির নজির কম।
অন্যদিকে, মাঝেমধ্যে দেখা যায় সরকার এমন আইন বা বিধান প্রণয়ন করে যেগুলো মূলত নিচতলার কর্মচারীদের উপর চাপে রাখার উপায় হয়ে দাঁড়ায়, অথচ উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি, অপব্যবস্থাপনা কিংবা সিদ্ধান্তহীনতা থেকে কেউই জবাবদিহির আওতায় আসে না।
একটি কার্যকর প্রশাসন গঠনের জন্য যে জবাবদিহিতা দরকার, সেটি হতে হবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, জবাবদিহিতা অনেকাংশেই একমুখী বা পক্ষপাতদুষ্ট। ফলে কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং আস্থার সংকট তৈরি হয়।
বিক্ষোভ কেন?
বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের আয়োজনে হওয়া এই বিক্ষোভ শুধু চাকরি বাঁচানোর জন্য নয়, এটি চাকরির নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার আন্দোলন। তারা চাইছেন:
- অধ্যাদেশটি অবিলম্বে বাতিল বা পুনর্বিবেচনা করতে হবে;
- দমনমূলক শাস্তি নয়, বরং মানবিক ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে;
- উচ্চপর্যায়ের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে;
- কর্মীদের ন্যায্য অধিকার ও আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
সরেজমিন দেখা যায়, শত শত কর্মচারী অফিস ফেলে নিচে নেমে আসেন, শ্লোগান দেন—“অবৈধ কালো আইন মানি না, মানব না”, “দমননীতি চলবে না”, ইত্যাদি। সচিবালয়ের ভেতরে তারা ঘুরে ঘুরে মিছিল করে এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।
কী হতে পারে গ্রহণযোগ্য সমাধান?
একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় চাকরিজীবীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা জরুরি। কিন্তু সেটি হতে হবে:
- সহানুভূতিশীল ও বিচারযোগ্য পদ্ধতিতে, যেখানে শুনানি ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে;
- সুষম ও নিরপেক্ষভাবে, যাতে শুধু নিচতলা নয়, উপরের কর্মকর্তারাও জবাবদিহির আওতায় আসেন;
- আইনি নিরপত্তা ও সাংবিধানিক অধিকার বজায় রেখে, যাতে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।
সরকার চাইলে কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে অধ্যাদেশটির বিতর্কিত ধারাগুলোর যৌক্তিক পর্যালোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য, কর্মবান্ধব আইন প্রণয়ন করতে পারে। এতে যেমন প্রশাসনের স্বচ্ছতা বাড়বে, তেমনি কর্মীদের মনোবলও বাড়বে।
চাকরিতে জবাবদিহিতা জরুরি, তবে সেটি যেন ন্যায়সঙ্গত, মানবিক এবং সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য হয়। আইন প্রয়োগে বৈষম্য বা একতরফা দমননীতি প্রশাসনের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত সেবার মান কমিয়ে দেয়, জনগণের প্রতি আস্থা নষ্ট করে।
‘সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫’-এর নামে যদি কর্মীদের মৌলিক অধিকার হরণ হয়, তবে সেটি একটি কালাকানুন হিসেবেই বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন কর্মীবান্ধব, স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো, যেখানে নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গে মানবিকতা ও ন্যায়ের সুষম মিশ্রণ থাকবে। সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সাংবিধানিক আদর্শের ভিত্তিতেই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব।
@billal hossain
Please Share This Post in Your Social Media

কালাকানুন’ নাকি সংস্কার? সরকারি চাকরি সংশোধনী আইন ঘিরে বিতর্ক


নির্বাচনকালীন সরকার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সম্প্রতি অনুমোদিত ‘সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ নিয়ে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তা শুধু একটি আইন বা বিধির বিরুদ্ধে ক্ষোভ নয়—এটি বাংলাদেশের কর্মপরিবেশ ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের অসামঞ্জস্যতার প্রতিচ্ছবি।
বাংলাদেশে প্রতিটি চাকরির—হোক তা সরকারি, বেসরকারি কিংবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে—অধিকার যেমন আছে, তেমনি রয়েছে কর্তব্য এবং জবাবদিহিতা। তবে বাস্তবতা হলো, কর্মক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ, জবাবদিহিতা এবং দায়িত্বশীলতা এখনও অনেকাংশে কাগুজে রয়ে গেছে। বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে কর্মরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হলেও বাস্তব প্রয়োগে দেখা যায় পক্ষপাতদুষ্টতা, দীর্ঘসূত্রিতা এবং অনিয়ম।
সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত ‘সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর খসড়াকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্নগুলো আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। আইনটির বিরুদ্ধে গত কয়েক দিন ধরে সচিবালয়ে হাজার হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী দপ্তর ছেড়ে বিক্ষোভ করেছেন। তারা এই অধ্যাদেশকে ‘কালাকানুন’ আখ্যা দিয়ে প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন। এই আন্দোলন কোনো সাধারণ বেতনবৃদ্ধি বা সুযোগ-সুবিধার দাবিনির্ভর নয়, বরং এটি একটি মৌলিক ও গভীর শঙ্কার বহিঃপ্রকাশ—চাকরিজীবীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন।
অধ্যাদেশটি কী বলছে?
সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর কিছু বিধান সংশোধন করে তৈরি এই খসড়া অধ্যাদেশে কিছু ‘নিবর্তনমূলক’ ধারা যুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে—
- কর্মচারী কর্তব্যে অবহেলা বা অসদাচরণ করলে তাদের বিরুদ্ধে সহজে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
- কোনো ধরনের শুনানি ছাড়াই সাময়িক বরখাস্ত বা চাকরিচ্যুতির ক্ষমতা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।
- প্রক্রিয়াগত জটিলতা এড়াতে ‘ত্বরিত বিচার’ ব্যবস্থার মতো নিয়ম যোগ করা হয়েছে যা অসদ্ব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি বহন করে।
বর্তমান কর্মচারীদের অভিযোগ, আধুনিক সময়ের জন্য এই ধারা অত্যন্ত অমানবিক এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী। তারা বলছেন, এই অধ্যাদেশ সংবিধানের ২৬, ২৭ ও ৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী, যেখানে সমতা, ন্যায্যতা ও আইনগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
বাস্তবতা: জবাবদিহিতার অভাব নাকি বৈষম্য?
বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি চাকরিতে কিছু অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। নিম্নস্তরের কর্মচারীরা নানা কারণে শাস্তি পেয়ে থাকেন, কিন্তু উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রায়শই দায় এড়াতে সক্ষম হন। উদাহরণ হিসেবে, ফাইল আটকে রাখা, ঘুষ নেওয়া, দাপ্তরিক বিলম্ব—এসব বিষয়ে শত শত অভিযোগ জমা থাকলেও, প্রকৃত শাস্তির নজির কম।
অন্যদিকে, মাঝেমধ্যে দেখা যায় সরকার এমন আইন বা বিধান প্রণয়ন করে যেগুলো মূলত নিচতলার কর্মচারীদের উপর চাপে রাখার উপায় হয়ে দাঁড়ায়, অথচ উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি, অপব্যবস্থাপনা কিংবা সিদ্ধান্তহীনতা থেকে কেউই জবাবদিহির আওতায় আসে না।
একটি কার্যকর প্রশাসন গঠনের জন্য যে জবাবদিহিতা দরকার, সেটি হতে হবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, জবাবদিহিতা অনেকাংশেই একমুখী বা পক্ষপাতদুষ্ট। ফলে কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং আস্থার সংকট তৈরি হয়।
বিক্ষোভ কেন?
বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের আয়োজনে হওয়া এই বিক্ষোভ শুধু চাকরি বাঁচানোর জন্য নয়, এটি চাকরির নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার আন্দোলন। তারা চাইছেন:
- অধ্যাদেশটি অবিলম্বে বাতিল বা পুনর্বিবেচনা করতে হবে;
- দমনমূলক শাস্তি নয়, বরং মানবিক ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে;
- উচ্চপর্যায়ের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে;
- কর্মীদের ন্যায্য অধিকার ও আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
সরেজমিন দেখা যায়, শত শত কর্মচারী অফিস ফেলে নিচে নেমে আসেন, শ্লোগান দেন—“অবৈধ কালো আইন মানি না, মানব না”, “দমননীতি চলবে না”, ইত্যাদি। সচিবালয়ের ভেতরে তারা ঘুরে ঘুরে মিছিল করে এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।
কী হতে পারে গ্রহণযোগ্য সমাধান?
একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় চাকরিজীবীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা জরুরি। কিন্তু সেটি হতে হবে:
- সহানুভূতিশীল ও বিচারযোগ্য পদ্ধতিতে, যেখানে শুনানি ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে;
- সুষম ও নিরপেক্ষভাবে, যাতে শুধু নিচতলা নয়, উপরের কর্মকর্তারাও জবাবদিহির আওতায় আসেন;
- আইনি নিরপত্তা ও সাংবিধানিক অধিকার বজায় রেখে, যাতে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।
সরকার চাইলে কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে অধ্যাদেশটির বিতর্কিত ধারাগুলোর যৌক্তিক পর্যালোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য, কর্মবান্ধব আইন প্রণয়ন করতে পারে। এতে যেমন প্রশাসনের স্বচ্ছতা বাড়বে, তেমনি কর্মীদের মনোবলও বাড়বে।
চাকরিতে জবাবদিহিতা জরুরি, তবে সেটি যেন ন্যায়সঙ্গত, মানবিক এবং সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য হয়। আইন প্রয়োগে বৈষম্য বা একতরফা দমননীতি প্রশাসনের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত সেবার মান কমিয়ে দেয়, জনগণের প্রতি আস্থা নষ্ট করে।
‘সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫’-এর নামে যদি কর্মীদের মৌলিক অধিকার হরণ হয়, তবে সেটি একটি কালাকানুন হিসেবেই বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন কর্মীবান্ধব, স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো, যেখানে নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গে মানবিকতা ও ন্যায়ের সুষম মিশ্রণ থাকবে। সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সাংবিধানিক আদর্শের ভিত্তিতেই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব।
@billal hossain