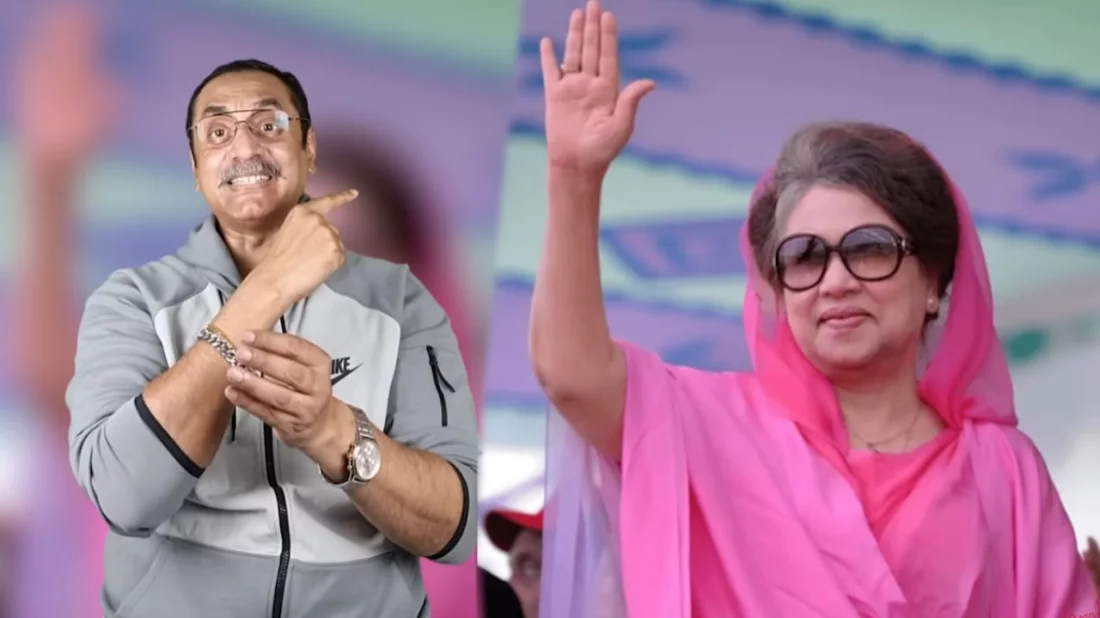রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং বাকস্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সংস্কার জরুরী
- Update Time : ০৭:১২:২০ পূর্বাহ্ন, শনিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৪
- / ৯২ Time View

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ছয়টি ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে, তবে “গোয়েন্দা বিভাগের সংস্কার” সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। অথচ এটি সংস্কারের জন্য প্রথম স্থান পাওয়ার যোগ্য ছিল। সম্প্রতি, সরকার যে পাঁচটি ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য কমিটি গঠন করেছে, সেগুলি হলো— ১. জনপ্রশাসন, ২. দুর্নীতি দমন, ৩. নির্বাচন কমিশন, ৪. বিচার বিভাগ, এবং ৫. পুলিশ বিভাগ। তবে এই সবক্ষেত্রের পেছনে যে শক্তিশালী অংশটি কাজ করে, সেটি হলো গোয়েন্দা বিভাগ, যা এখনও সংস্কারের বাইরে রয়ে গেছে।
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং বাকস্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। জুলাই মাসের গণ-অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান দুটি অর্থনৈতিক কারণ ছিল—বেকারত্ব এবং মূল্যস্ফীতি। এর সঙ্গে সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল বাকস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার চাওয়া। এই দাবিগুলো দমন করতে গত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগগুলো অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
গোয়েন্দারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হলেও তারা জনগণের টাকায় বেতন পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক ক্যাডার বাহিনীর মতো আচরণ করেছে, যা অসাংবিধানিক। এটি গোয়েন্দা সংস্থার আসল উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক। গোয়েন্দা বিভাগের এই অপব্যবহারের কারণে বাংলা সাহিত্যে ‘আয়নাঘর’ এবং ‘ভাতের হোটেল’-এর মতো বিষয়গুলো উঠে এসেছে, যা সাধারণ মানুষের মাঝে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।
আওয়ামী লীগের মতো একটি তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে আসা দল শেষ পর্যন্ত আমলা, ব্যবসায়ী এবং গোয়েন্দাদের প্রভাবের মধ্যে আটকে পড়েছিল। সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কার্যকরী প্রয়োগে ব্যর্থ হওয়ায় দলটি এমন দুঃখজনক বিদায়ের মুখোমুখি হয়েছে। এর পেছনে গোয়েন্দা বিভাগগুলোর বড় ধরনের ব্যর্থতাও অন্যতম কারণ ছিল, কারণ তারা ক্ষমতার অপব্যবহার, অপেশাদারি আচরণ এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে, এই বিভাগগুলোর দ্রুত সংস্কার এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
এই সংস্থাগুলোকে সংস্কারের বাইরে রেখে অন্য সব সংস্কার কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়বে, কারণ গোয়েন্দা বিভাগগুলোর প্রভাব ইতোমধ্যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী সরকারগুলোকেও এরা সহজেই প্রভাবিত করতে পারে। তখন নির্বাচিত সরকারও হয়তো ভাববে, বিরোধী দল বা ভিন্নমতের লোকদের দমন করতে গোয়েন্দাদের সহায়তা নেওয়া ক্ষতিকর হবে না। তখন ‘আয়নাঘর’ এর জায়গায় হয়তো ‘চিরুনিঘর’ আর ‘ভাতের হোটেল’ এর বদলে ‘ক্যাফে বিরিয়ানি’ চালু হবে।
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে বড় ধরনের সংস্কারের দাবি ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান বিশ্বরাজনীতিতে পরিবর্তন আনে, এবং মার্কিন কংগ্রেসে গোয়েন্দা কার্যক্রমের পুনঃসংজ্ঞায়ন শুরু হয়। সিনেটর ড্যানিয়েল মইনিহ্যান বলেছিলেন যে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-এর পুরোনো কাজের ধরন বদলাতে হবে এবং স্নায়ুযুদ্ধের যুগের কর্মকর্তাদের অবসর নেওয়ার সময় এসেছে।
উন্নত দেশগুলোর উত্তম চর্চা অনুসরণ করে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেন জ্ঞান ও গবেষণার মাধ্যমে দুর্নীতিপরায়ণদের দমন এবং সৎ ও যোগ্যদের রক্ষায় নিয়োজিত থাকে। তাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তা সুরক্ষা, এবং রাষ্ট্রের সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা জোরদার করা।
আসলে এই চিন্তা থেকেই বলা হয়েছে যে, সিআইএ তখন থেকে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির দিকে মনোযোগ দেয়। তখন চীন এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি, আর রাশিয়া ছিল দুর্বল অবস্থায়। তাই মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যে শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তিনটি মূল ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবে: ১. অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তি, ২. পরিবেশগত হুমকির মোকাবিলা, এবং ৩. অর্থ পাচার প্রতিরোধ। এই পরিকল্পনা ছিল বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করা।
মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সংস্কারের লক্ষ্যে সেই সময়ে একটি সিনেট কমিটি গঠিত হয়েছিল, যার চেয়ারম্যান ডেনিস ডিকনসিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে পরিবর্তিত বিশ্বে সামরিক যুদ্ধের চেয়ে বড় যুদ্ধ এখন অর্থনীতি ও প্রযুক্তির প্রতিযোগিতা। তার মতে, এই নতুন বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বদা এক ধাপ এগিয়ে রাখতে হবে, এবং এটাই হবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মূল কাজ।
কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজের ধরণ এবং তাদের অনলাইন উপস্থিতি পুরোপুরি বদলে যায়। তাদের ওয়েবসাইটগুলো এমনভাবে সাজানো হয়, যেন সেগুলো কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিআইডিএস-এর মতো কাজ করছে।
যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থা থাকলেও প্রধানত সিআইএ (সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি), এনএসএ (ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি), ডিআইএ (ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি), এবং এফবিআই (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) বেশি পরিচিত। যদিও সংখ্যাটি অনেক বেশি মনে হতে পারে, তবে প্রত্যেক সংস্থার কাজ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত।
বাংলাদেশে যেমন ‘ভাতের হোটেল’ বা ‘আয়নাঘর’-এর মতো একই ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের প্রচেষ্টা দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের ব্যবস্থা নেই। সেখানে অ্যাডাম স্মিথের শ্রমবিভাজন তত্ত্ব অনুসরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সিআইএ মূলত মানুষের কার্যকলাপ নিয়ে কাজ করে, আর এনএসএ সংকেত ও ইলেকট্রনিক গোয়েন্দাগিরিতে বিশেষজ্ঞ। তবে দিনের শেষে তাদের দুটোই কাজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কোনো রাজনৈতিক দলের শাসন দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্য নয়।
সিআইএ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা হলেও এর কার্যক্রম শুধুমাত্র বিদেশি নাগরিকদের সম্পর্কিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ। মার্কিন নাগরিকদের ওপর সিআইএর কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং গ্রেপ্তারের ক্ষমতাও নেই, যা শুধুমাত্র এফবিআইয়ের হাতে। সিআইএর মূল কাজ যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং গুপ্তচরবৃত্তি চালানো। বিভিন্ন পেশার কৌশলবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, উপাত্ত বিশ্লেষক, হিসাববিদ এবং গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত এই সংস্থাকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।
নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জন ন্যাশ তাঁর গেম থিওরির জন্য বিখ্যাত, যা কূটনীতি এবং সমরবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই কৌশল গোয়েন্দাবৃত্তিতেও প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং এ কারণেই ন্যাশ গোয়েন্দাবৃত্তির কৌশলে একজন সম্মানিত পণ্ডিত হিসেবে বিবেচিত হন। এভাবে গোয়েন্দাবিদ্যা নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেন অধঃপতনের শিকার হয়েছে। সরকারগুলো নিজেদের দলীয় স্বার্থে তাদের প্রায়শই ব্যবহার করেছে, ফলে তাদের কার্যকারিতা ও ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তাই এই সংস্থাগুলোর সংস্কার ও পুনর্গঠন এখন সময়ের দাবি।
বাংলাদেশে ডিজিএফআই, ডিবি, এসবিসহ বেশিরভাগ গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে যেন একটি অলিখিত প্রতিযোগিতা চলছে, যার মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষা করা। এই প্রতিযোগিতার প্রধান পরীক্ষা হচ্ছে, কে আগে তথাকথিত শত্রুপক্ষের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এমনকি ব্যক্তিগত জীবনের শয়নকক্ষের কথোপকথনও রেকর্ড করা হয়, যা অত্যন্ত অনুচিত এবং অগ্রহণযোগ্য। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তাকে লঙ্ঘন করে, যা মানবাধিকারের একটি অংশ।
ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা একটি মৌলিক অধিকার। এরকম একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে একজন মেধাবী ছাত্র, যার বিভাগীয় শিক্ষক হওয়ার সব যোগ্যতা ছিল, দুঃখের সঙ্গে জানায় যে ভাইভার আগের রাতে গোয়েন্দা সংস্থা থেকে তাকে ফোন করে মানসিক চাপে ফেলা হয়েছিল। তার রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যা তাকে আঘাত করে।
এটি কি আসলেই স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্র হওয়া উচিত? এই প্রশ্নটি এসে দাঁড়ায় যখন ঢাকার মতো প্রতিষ্ঠানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমন আচরণ কি পাকিস্তান আমলেও ছিল? নাকি এটা রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়ার মতো দেশের ছায়া পড়ছে আমাদের সমাজে? স্বাধীন বাংলাদেশের একটি প্রগতিশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের পরিস্থিতি জাতির জন্য লজ্জাজনক।
এখানেই সমস্যা শেষ নয়। চট্টগ্রামের প্রভাবশালী ব্যাংক লুটেরাদের সহায়তা দিয়ে কিভাবে আরও ব্যাংক ধ্বংস করা যায়, সেখানেও গোয়েন্দাদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। টক শোতে কাকে আনা যাবে এবং কাকে আনা যাবে না, এমনকি সংবাদপত্রে কী খবর প্রকাশ পাবে আর কী পাবে না—সবকিছুতে তাদের হস্তক্ষেপ স্পষ্ট। এমনকি সাবেক প্রধান বিচারপতিকে প্রচ্ছন্নভাবে চাপ দিয়ে দেশ ছাড়াতে চেষ্টার ক্ষেত্রেও তাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যদি এভাবে চলতে থাকে, কিছুদিনের মধ্যে তারা হয়তো ঠিক করবে কার সঙ্গে কার বিয়ে বা বিচ্ছেদ হবে।
এই অশুভ সংকেত বোঝায় যে ক্ষমতার লোভে লিপ্ত সরকারি দলের প্রভাবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্যের সেই ‘পথভোলা পথিক’-এর মতো দিকভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাই গোয়েন্দা বিভাগের সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের কাজের একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা তৈরি করা, যাতে পেশাদারি বাড়ে এবং তারা আসল কাজ—রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা—নির্ভুলভাবে করতে পারে।
উন্নত দেশের সেরা অভ্যাসগুলো অনুসরণ করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে জ্ঞান এবং গবেষণার মাধ্যমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নিশ্চিত করে রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এর পাশাপাশি, মানুষের মৌলিক অধিকার এবং ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করা, এবং রাষ্ট্রের সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা বৃদ্ধি করাই তাদের সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।
নিচে উল্লিখিত প্রবন্ধের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎসের তালিকা:
১. সাংবিধানিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা
– সত্তরের সংবিধান: “বাংলাদেশের সংবিধান” – [বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রণালয়](http://www.mola.gov.bd/)
– গবেষণা পত্র: “বাকস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র” – রবিশঙ্কর শীল
২. প্রথম আলো -মতামত কলাম-সবার আগে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সংস্কার কেন দরকার-ড. বিরূপাক্ষ পাল যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক অ্যাট কোর্টল্যান্ড-এ অর্থনীতির অধ্যাপক
৩. গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম ও সংস্কার
– “বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যক্রম: এক বিশ্লেষণ” – মাসুদ করিম
– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্কারের উপর গবেষণা: “The New Intelligence Paradigm” – ডেনিস ডিকনসিনি
৪. মানবাধিকার ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা
– জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন
– গবেষণা পত্র: “বাংলাদেশে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার” – শ্রীমতি আঞ্জলি
৫. আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি
– “সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর: বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তন” – অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম
– কংগ্রেসের আলোচনা: “Intelligence Oversight and Reform” – মার্কিন কংগ্রেস
৬. বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত
– বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন
– “বাংলাদেশে ব্যাংক লুট: একটি বিশ্লেষণ” – ড. কামাল হোসেন
৭. গোয়েন্দা বিভাগে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা
– “Why Intelligence Reform Matters” – গবেষণা পত্র, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
– “The Role of Intelligence in National Security” – গবেষণা, র্যান্ড কর্পোরেশন
৮. জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন
– “জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি: রাজনীতি ও গোয়েন্দা কার্যক্রম” – জরিপ প্রতিবেদন, সিএসসি
৯. অর্থনীতি ও সামাজিক গবেষণা
– বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) প্রতিবেদন
– বিশ্বব্যাংক: “বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ২০২৪”
Please Share This Post in Your Social Media

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং বাকস্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সংস্কার জরুরী


বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ছয়টি ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে, তবে “গোয়েন্দা বিভাগের সংস্কার” সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। অথচ এটি সংস্কারের জন্য প্রথম স্থান পাওয়ার যোগ্য ছিল। সম্প্রতি, সরকার যে পাঁচটি ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য কমিটি গঠন করেছে, সেগুলি হলো— ১. জনপ্রশাসন, ২. দুর্নীতি দমন, ৩. নির্বাচন কমিশন, ৪. বিচার বিভাগ, এবং ৫. পুলিশ বিভাগ। তবে এই সবক্ষেত্রের পেছনে যে শক্তিশালী অংশটি কাজ করে, সেটি হলো গোয়েন্দা বিভাগ, যা এখনও সংস্কারের বাইরে রয়ে গেছে।
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং বাকস্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। জুলাই মাসের গণ-অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান দুটি অর্থনৈতিক কারণ ছিল—বেকারত্ব এবং মূল্যস্ফীতি। এর সঙ্গে সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল বাকস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার চাওয়া। এই দাবিগুলো দমন করতে গত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগগুলো অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
গোয়েন্দারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হলেও তারা জনগণের টাকায় বেতন পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক ক্যাডার বাহিনীর মতো আচরণ করেছে, যা অসাংবিধানিক। এটি গোয়েন্দা সংস্থার আসল উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক। গোয়েন্দা বিভাগের এই অপব্যবহারের কারণে বাংলা সাহিত্যে ‘আয়নাঘর’ এবং ‘ভাতের হোটেল’-এর মতো বিষয়গুলো উঠে এসেছে, যা সাধারণ মানুষের মাঝে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।
আওয়ামী লীগের মতো একটি তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে আসা দল শেষ পর্যন্ত আমলা, ব্যবসায়ী এবং গোয়েন্দাদের প্রভাবের মধ্যে আটকে পড়েছিল। সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কার্যকরী প্রয়োগে ব্যর্থ হওয়ায় দলটি এমন দুঃখজনক বিদায়ের মুখোমুখি হয়েছে। এর পেছনে গোয়েন্দা বিভাগগুলোর বড় ধরনের ব্যর্থতাও অন্যতম কারণ ছিল, কারণ তারা ক্ষমতার অপব্যবহার, অপেশাদারি আচরণ এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে, এই বিভাগগুলোর দ্রুত সংস্কার এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
এই সংস্থাগুলোকে সংস্কারের বাইরে রেখে অন্য সব সংস্কার কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়বে, কারণ গোয়েন্দা বিভাগগুলোর প্রভাব ইতোমধ্যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী সরকারগুলোকেও এরা সহজেই প্রভাবিত করতে পারে। তখন নির্বাচিত সরকারও হয়তো ভাববে, বিরোধী দল বা ভিন্নমতের লোকদের দমন করতে গোয়েন্দাদের সহায়তা নেওয়া ক্ষতিকর হবে না। তখন ‘আয়নাঘর’ এর জায়গায় হয়তো ‘চিরুনিঘর’ আর ‘ভাতের হোটেল’ এর বদলে ‘ক্যাফে বিরিয়ানি’ চালু হবে।
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে বড় ধরনের সংস্কারের দাবি ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান বিশ্বরাজনীতিতে পরিবর্তন আনে, এবং মার্কিন কংগ্রেসে গোয়েন্দা কার্যক্রমের পুনঃসংজ্ঞায়ন শুরু হয়। সিনেটর ড্যানিয়েল মইনিহ্যান বলেছিলেন যে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-এর পুরোনো কাজের ধরন বদলাতে হবে এবং স্নায়ুযুদ্ধের যুগের কর্মকর্তাদের অবসর নেওয়ার সময় এসেছে।
উন্নত দেশগুলোর উত্তম চর্চা অনুসরণ করে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেন জ্ঞান ও গবেষণার মাধ্যমে দুর্নীতিপরায়ণদের দমন এবং সৎ ও যোগ্যদের রক্ষায় নিয়োজিত থাকে। তাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তা সুরক্ষা, এবং রাষ্ট্রের সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা জোরদার করা।
আসলে এই চিন্তা থেকেই বলা হয়েছে যে, সিআইএ তখন থেকে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির দিকে মনোযোগ দেয়। তখন চীন এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি, আর রাশিয়া ছিল দুর্বল অবস্থায়। তাই মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যে শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তিনটি মূল ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবে: ১. অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তি, ২. পরিবেশগত হুমকির মোকাবিলা, এবং ৩. অর্থ পাচার প্রতিরোধ। এই পরিকল্পনা ছিল বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করা।
মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সংস্কারের লক্ষ্যে সেই সময়ে একটি সিনেট কমিটি গঠিত হয়েছিল, যার চেয়ারম্যান ডেনিস ডিকনসিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে পরিবর্তিত বিশ্বে সামরিক যুদ্ধের চেয়ে বড় যুদ্ধ এখন অর্থনীতি ও প্রযুক্তির প্রতিযোগিতা। তার মতে, এই নতুন বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বদা এক ধাপ এগিয়ে রাখতে হবে, এবং এটাই হবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মূল কাজ।
কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজের ধরণ এবং তাদের অনলাইন উপস্থিতি পুরোপুরি বদলে যায়। তাদের ওয়েবসাইটগুলো এমনভাবে সাজানো হয়, যেন সেগুলো কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিআইডিএস-এর মতো কাজ করছে।
যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থা থাকলেও প্রধানত সিআইএ (সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি), এনএসএ (ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি), ডিআইএ (ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি), এবং এফবিআই (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) বেশি পরিচিত। যদিও সংখ্যাটি অনেক বেশি মনে হতে পারে, তবে প্রত্যেক সংস্থার কাজ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত।
বাংলাদেশে যেমন ‘ভাতের হোটেল’ বা ‘আয়নাঘর’-এর মতো একই ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের প্রচেষ্টা দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের ব্যবস্থা নেই। সেখানে অ্যাডাম স্মিথের শ্রমবিভাজন তত্ত্ব অনুসরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সিআইএ মূলত মানুষের কার্যকলাপ নিয়ে কাজ করে, আর এনএসএ সংকেত ও ইলেকট্রনিক গোয়েন্দাগিরিতে বিশেষজ্ঞ। তবে দিনের শেষে তাদের দুটোই কাজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কোনো রাজনৈতিক দলের শাসন দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্য নয়।
সিআইএ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা হলেও এর কার্যক্রম শুধুমাত্র বিদেশি নাগরিকদের সম্পর্কিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ। মার্কিন নাগরিকদের ওপর সিআইএর কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং গ্রেপ্তারের ক্ষমতাও নেই, যা শুধুমাত্র এফবিআইয়ের হাতে। সিআইএর মূল কাজ যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং গুপ্তচরবৃত্তি চালানো। বিভিন্ন পেশার কৌশলবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, উপাত্ত বিশ্লেষক, হিসাববিদ এবং গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত এই সংস্থাকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।
নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জন ন্যাশ তাঁর গেম থিওরির জন্য বিখ্যাত, যা কূটনীতি এবং সমরবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই কৌশল গোয়েন্দাবৃত্তিতেও প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং এ কারণেই ন্যাশ গোয়েন্দাবৃত্তির কৌশলে একজন সম্মানিত পণ্ডিত হিসেবে বিবেচিত হন। এভাবে গোয়েন্দাবিদ্যা নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেন অধঃপতনের শিকার হয়েছে। সরকারগুলো নিজেদের দলীয় স্বার্থে তাদের প্রায়শই ব্যবহার করেছে, ফলে তাদের কার্যকারিতা ও ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তাই এই সংস্থাগুলোর সংস্কার ও পুনর্গঠন এখন সময়ের দাবি।
বাংলাদেশে ডিজিএফআই, ডিবি, এসবিসহ বেশিরভাগ গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে যেন একটি অলিখিত প্রতিযোগিতা চলছে, যার মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষা করা। এই প্রতিযোগিতার প্রধান পরীক্ষা হচ্ছে, কে আগে তথাকথিত শত্রুপক্ষের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এমনকি ব্যক্তিগত জীবনের শয়নকক্ষের কথোপকথনও রেকর্ড করা হয়, যা অত্যন্ত অনুচিত এবং অগ্রহণযোগ্য। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তাকে লঙ্ঘন করে, যা মানবাধিকারের একটি অংশ।
ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা একটি মৌলিক অধিকার। এরকম একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে একজন মেধাবী ছাত্র, যার বিভাগীয় শিক্ষক হওয়ার সব যোগ্যতা ছিল, দুঃখের সঙ্গে জানায় যে ভাইভার আগের রাতে গোয়েন্দা সংস্থা থেকে তাকে ফোন করে মানসিক চাপে ফেলা হয়েছিল। তার রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যা তাকে আঘাত করে।
এটি কি আসলেই স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্র হওয়া উচিত? এই প্রশ্নটি এসে দাঁড়ায় যখন ঢাকার মতো প্রতিষ্ঠানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমন আচরণ কি পাকিস্তান আমলেও ছিল? নাকি এটা রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়ার মতো দেশের ছায়া পড়ছে আমাদের সমাজে? স্বাধীন বাংলাদেশের একটি প্রগতিশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের পরিস্থিতি জাতির জন্য লজ্জাজনক।
এখানেই সমস্যা শেষ নয়। চট্টগ্রামের প্রভাবশালী ব্যাংক লুটেরাদের সহায়তা দিয়ে কিভাবে আরও ব্যাংক ধ্বংস করা যায়, সেখানেও গোয়েন্দাদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। টক শোতে কাকে আনা যাবে এবং কাকে আনা যাবে না, এমনকি সংবাদপত্রে কী খবর প্রকাশ পাবে আর কী পাবে না—সবকিছুতে তাদের হস্তক্ষেপ স্পষ্ট। এমনকি সাবেক প্রধান বিচারপতিকে প্রচ্ছন্নভাবে চাপ দিয়ে দেশ ছাড়াতে চেষ্টার ক্ষেত্রেও তাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যদি এভাবে চলতে থাকে, কিছুদিনের মধ্যে তারা হয়তো ঠিক করবে কার সঙ্গে কার বিয়ে বা বিচ্ছেদ হবে।
এই অশুভ সংকেত বোঝায় যে ক্ষমতার লোভে লিপ্ত সরকারি দলের প্রভাবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্যের সেই ‘পথভোলা পথিক’-এর মতো দিকভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাই গোয়েন্দা বিভাগের সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের কাজের একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা তৈরি করা, যাতে পেশাদারি বাড়ে এবং তারা আসল কাজ—রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা—নির্ভুলভাবে করতে পারে।
উন্নত দেশের সেরা অভ্যাসগুলো অনুসরণ করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে জ্ঞান এবং গবেষণার মাধ্যমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নিশ্চিত করে রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এর পাশাপাশি, মানুষের মৌলিক অধিকার এবং ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করা, এবং রাষ্ট্রের সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা বৃদ্ধি করাই তাদের সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।
নিচে উল্লিখিত প্রবন্ধের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎসের তালিকা:
১. সাংবিধানিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা
– সত্তরের সংবিধান: “বাংলাদেশের সংবিধান” – [বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রণালয়](http://www.mola.gov.bd/)
– গবেষণা পত্র: “বাকস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র” – রবিশঙ্কর শীল
২. প্রথম আলো -মতামত কলাম-সবার আগে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সংস্কার কেন দরকার-ড. বিরূপাক্ষ পাল যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক অ্যাট কোর্টল্যান্ড-এ অর্থনীতির অধ্যাপক
৩. গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম ও সংস্কার
– “বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যক্রম: এক বিশ্লেষণ” – মাসুদ করিম
– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্কারের উপর গবেষণা: “The New Intelligence Paradigm” – ডেনিস ডিকনসিনি
৪. মানবাধিকার ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা
– জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন
– গবেষণা পত্র: “বাংলাদেশে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার” – শ্রীমতি আঞ্জলি
৫. আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি
– “সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর: বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তন” – অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম
– কংগ্রেসের আলোচনা: “Intelligence Oversight and Reform” – মার্কিন কংগ্রেস
৬. বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত
– বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন
– “বাংলাদেশে ব্যাংক লুট: একটি বিশ্লেষণ” – ড. কামাল হোসেন
৭. গোয়েন্দা বিভাগে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা
– “Why Intelligence Reform Matters” – গবেষণা পত্র, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
– “The Role of Intelligence in National Security” – গবেষণা, র্যান্ড কর্পোরেশন
৮. জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন
– “জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি: রাজনীতি ও গোয়েন্দা কার্যক্রম” – জরিপ প্রতিবেদন, সিএসসি
৯. অর্থনীতি ও সামাজিক গবেষণা
– বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) প্রতিবেদন
– বিশ্বব্যাংক: “বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ২০২৪”