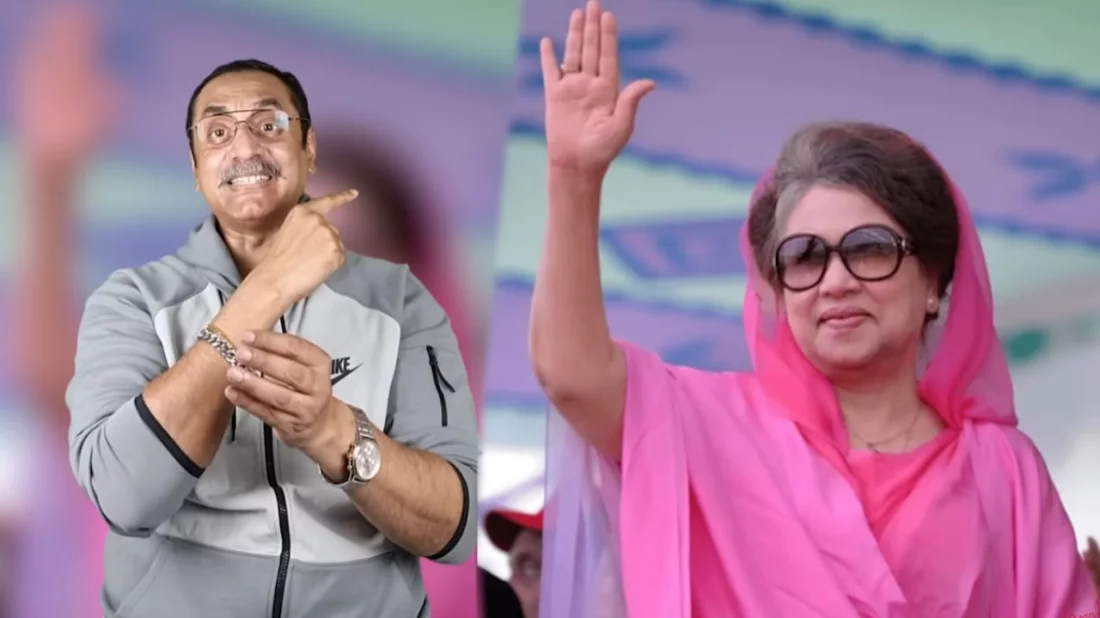১০ হাজার কোটি টাকার ‘বিলাসী’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কী?
- Update Time : ১১:২৪:০৪ অপরাহ্ন, বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪
- / ১০৯ Time View

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৩টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তারপরও শুধুমাত্র ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ স্লোগানের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনুমোদন দিয়েই শেষ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাবও আনা হয়েছিল। যদিও সমালোচনার কারণে সেই প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়নি।
শিক্ষাবিদ ও খাত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রকল্পটি ছিল মূলত একটি বিলাসী উদ্যোগ, যার পেছনে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য ছিল। দেশে যথেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও এমন একটি প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োজন নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল নামের আড়ালে হাজার কোটি টাকা লোপাটের চেষ্টাও ছিল প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।
২০১৬ সালে সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইন পাস হয়। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক সংলগ্ন ৫০ একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। ‘বিডিইউ’ এর কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় শুরু হয় ২০১৮ সালের জুনে।
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অংশগ্রহণ, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে অনলাইন শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া। উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎকর্ষ সাধনও ছিল এর লক্ষ্য।
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১,৪৬১ কোটি টাকা। গাজীপুরের কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্কের পাশে এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হবে, যেখানে হাইটেক পার্ক কেন্দ্রিক সকল প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করতেন সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক।
২০১৪/১৫ সালে প্রযুক্তি খাতে উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিকুলাম আপগ্রেডেশনের পরিকল্পনা করা হয়। সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম, রোবটিক্স, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, এডুকেশনাল টেকনোলজি, সফটওয়্যার অ্যান্ড মেশিন ইন্টেলিজেন্স, এবং ডাটা সাইন্সের মতো বিষয়গুলো প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। কিন্তু ২০১৫ সালে আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব আসে এবং কারিকুলাম আপগ্রেডেশনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সুপারিশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রস্তাবিত হয়। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা মাস্টার প্ল্যান ছিল না এবং শুরুতেই কোনো কাঠামো বা প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম কার্যক্রম শুরু হয় ঢাকায় ভাড়া করা ভবনে এবং প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নূর নিয়োগ পান।

ড. মুনাজ আহমেদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বিলাসী বাজেট প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছিল নেত্রকোনার শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যার ব্যয় ছিল ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা এবং জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ২০০ একর। কিন্তু গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় মাত্র ৫০ একর জমির ওপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয় ১০ হাজার ১০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো খাতে ব্যয় ধরা হয় ৪ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা এবং বাকি টাকা কেনাকাটায় খরচ হওয়ার কথা ছিল।
এই বিপুল ব্যয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (ডিপিপি) ২০২২ সালে মানবজমিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয় এবং মুনাজ আহমেদের স্থলে অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম ভিসির দায়িত্ব পান। মাহফুজুল ইসলাম ২০২৩ সালে ডিপিপির আংশিক বাজেট ৬৯৩ কোটি টাকার প্রস্তাব করেন, কিন্তু এর রিভিউ রিপোর্ট আসার আগেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে।
বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম ডিজিটাল হলেও বাস্তবে সাধারণ সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৫৯ জন, অথচ দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরেও এটি নিজস্ব ভবন ও ক্যাম্পাস পায়নি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম দুটি ভাড়া করা ভবনে চলছে এবং শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য বাসা ভাড়া নিয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষের অভাবে ছোট ছোট কক্ষে গাদাগাদি করে ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। এ বছর শেষে একটি ব্যাচ অনার্স শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ভবন বা অন্যান্য সুবিধা এখনও নির্মিত হয়নি।
শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ মাসের সেমিস্টার ফি বর্তমানে সাত হাজার টাকা থেকে ১২ হাজার টাকা করা হয়েছে। অকৃতকার্য হলে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ২১ হাজার টাকা দিতে হয়। তাদের অভিযোগ, প্রযুক্তিগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রাকটিক্যাল কার্যক্রমের পরিমাণ নগণ্য।
২০২২ সালের ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীপ্রতি ব্যয় সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার্থীপ্রতি ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে সাড়ে সাত লাখ টাকা, যা আগের বছরে ছিল নয় লাখ ২৫ হাজার টাকা।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ সাবির মন্তব্য করেছেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রযুক্তিগত কারিকুলাম আপডেট করা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বমানের শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এ পরিবর্তন আনতেই হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী অমিত হাসান, যিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় শিক্ষা ও গবেষণায় পিএইচডি করছেন, বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে তৈরি হওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানো উচিত নয়। এতে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র ঘাটতির মুখে পড়বে না, বরং ভবিষ্যতে হীনমন্যতায় ভুগতে পারে। বাংলাদেশের জন্য বর্তমানে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলোই যথেষ্ট; নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত রুট লেভেলে শিক্ষার উন্নয়নে মনোযোগ দেয়া।
অমিত হাসান আরও বলেন, গত সরকারের মান উন্নয়নের ধারণা ছিল নতুন ভবন নির্মাণ। এটি শুধুমাত্র দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রদর্শন করে, যা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটায় না বরং আত্মবিশ্বাসহীন গ্রাজুয়েট তৈরি করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রস্তাবের পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অর্থ লোপাট। যদি তারা সত্যিকারভাবে দেশকে ডিজিটাল করতে চাইতো, তবে প্রান্তিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা বিস্তার করতো। প্রতিটি জেলায় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা জরুরি। বর্তমানে বিপুল পরিমাণ মানুষ প্রবাসে আনস্কিলড হয়ে যাচ্ছে, যা কারিগরি শিক্ষার অভাবের ফল। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রতিযোগিতা মূলত টাকা নষ্ট করার একটি কৌশল, যেখানে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অকার্যকর হয়ে পড়ছে।
তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য উপরের স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আগে রুট লেভেলে আপডেট করা জরুরি। আগের সরকার নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল, যা আসলে লুটপাটের উদ্দেশ্যেই ছিল।
Please Share This Post in Your Social Media

১০ হাজার কোটি টাকার ‘বিলাসী’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কী?


বাংলাদেশে বর্তমানে ১৩টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তারপরও শুধুমাত্র ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ স্লোগানের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনুমোদন দিয়েই শেষ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাবও আনা হয়েছিল। যদিও সমালোচনার কারণে সেই প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়নি।
শিক্ষাবিদ ও খাত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রকল্পটি ছিল মূলত একটি বিলাসী উদ্যোগ, যার পেছনে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য ছিল। দেশে যথেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও এমন একটি প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োজন নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল নামের আড়ালে হাজার কোটি টাকা লোপাটের চেষ্টাও ছিল প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।
২০১৬ সালে সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইন পাস হয়। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক সংলগ্ন ৫০ একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। ‘বিডিইউ’ এর কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় শুরু হয় ২০১৮ সালের জুনে।
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অংশগ্রহণ, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে অনলাইন শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া। উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎকর্ষ সাধনও ছিল এর লক্ষ্য।
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১,৪৬১ কোটি টাকা। গাজীপুরের কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্কের পাশে এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হবে, যেখানে হাইটেক পার্ক কেন্দ্রিক সকল প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করতেন সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক।
২০১৪/১৫ সালে প্রযুক্তি খাতে উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিকুলাম আপগ্রেডেশনের পরিকল্পনা করা হয়। সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম, রোবটিক্স, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, এডুকেশনাল টেকনোলজি, সফটওয়্যার অ্যান্ড মেশিন ইন্টেলিজেন্স, এবং ডাটা সাইন্সের মতো বিষয়গুলো প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। কিন্তু ২০১৫ সালে আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব আসে এবং কারিকুলাম আপগ্রেডেশনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সুপারিশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রস্তাবিত হয়। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা মাস্টার প্ল্যান ছিল না এবং শুরুতেই কোনো কাঠামো বা প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম কার্যক্রম শুরু হয় ঢাকায় ভাড়া করা ভবনে এবং প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নূর নিয়োগ পান।

ড. মুনাজ আহমেদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বিলাসী বাজেট প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছিল নেত্রকোনার শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যার ব্যয় ছিল ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা এবং জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ২০০ একর। কিন্তু গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় মাত্র ৫০ একর জমির ওপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয় ১০ হাজার ১০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো খাতে ব্যয় ধরা হয় ৪ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা এবং বাকি টাকা কেনাকাটায় খরচ হওয়ার কথা ছিল।
এই বিপুল ব্যয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (ডিপিপি) ২০২২ সালে মানবজমিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয় এবং মুনাজ আহমেদের স্থলে অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম ভিসির দায়িত্ব পান। মাহফুজুল ইসলাম ২০২৩ সালে ডিপিপির আংশিক বাজেট ৬৯৩ কোটি টাকার প্রস্তাব করেন, কিন্তু এর রিভিউ রিপোর্ট আসার আগেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে।
বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম ডিজিটাল হলেও বাস্তবে সাধারণ সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৫৯ জন, অথচ দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরেও এটি নিজস্ব ভবন ও ক্যাম্পাস পায়নি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম দুটি ভাড়া করা ভবনে চলছে এবং শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য বাসা ভাড়া নিয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষের অভাবে ছোট ছোট কক্ষে গাদাগাদি করে ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। এ বছর শেষে একটি ব্যাচ অনার্স শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ভবন বা অন্যান্য সুবিধা এখনও নির্মিত হয়নি।
শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ মাসের সেমিস্টার ফি বর্তমানে সাত হাজার টাকা থেকে ১২ হাজার টাকা করা হয়েছে। অকৃতকার্য হলে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ২১ হাজার টাকা দিতে হয়। তাদের অভিযোগ, প্রযুক্তিগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রাকটিক্যাল কার্যক্রমের পরিমাণ নগণ্য।
২০২২ সালের ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীপ্রতি ব্যয় সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার্থীপ্রতি ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে সাড়ে সাত লাখ টাকা, যা আগের বছরে ছিল নয় লাখ ২৫ হাজার টাকা।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ সাবির মন্তব্য করেছেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রযুক্তিগত কারিকুলাম আপডেট করা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বমানের শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এ পরিবর্তন আনতেই হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী অমিত হাসান, যিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় শিক্ষা ও গবেষণায় পিএইচডি করছেন, বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে তৈরি হওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানো উচিত নয়। এতে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র ঘাটতির মুখে পড়বে না, বরং ভবিষ্যতে হীনমন্যতায় ভুগতে পারে। বাংলাদেশের জন্য বর্তমানে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলোই যথেষ্ট; নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত রুট লেভেলে শিক্ষার উন্নয়নে মনোযোগ দেয়া।
অমিত হাসান আরও বলেন, গত সরকারের মান উন্নয়নের ধারণা ছিল নতুন ভবন নির্মাণ। এটি শুধুমাত্র দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রদর্শন করে, যা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটায় না বরং আত্মবিশ্বাসহীন গ্রাজুয়েট তৈরি করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রস্তাবের পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অর্থ লোপাট। যদি তারা সত্যিকারভাবে দেশকে ডিজিটাল করতে চাইতো, তবে প্রান্তিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা বিস্তার করতো। প্রতিটি জেলায় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা জরুরি। বর্তমানে বিপুল পরিমাণ মানুষ প্রবাসে আনস্কিলড হয়ে যাচ্ছে, যা কারিগরি শিক্ষার অভাবের ফল। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রতিযোগিতা মূলত টাকা নষ্ট করার একটি কৌশল, যেখানে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অকার্যকর হয়ে পড়ছে।
তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য উপরের স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আগে রুট লেভেলে আপডেট করা জরুরি। আগের সরকার নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল, যা আসলে লুটপাটের উদ্দেশ্যেই ছিল।